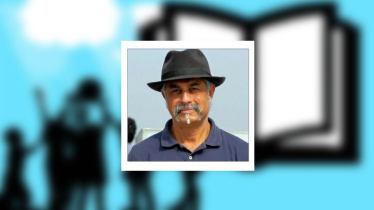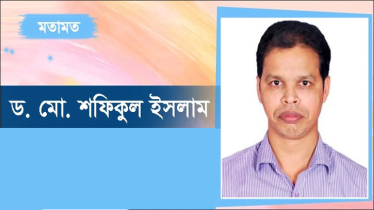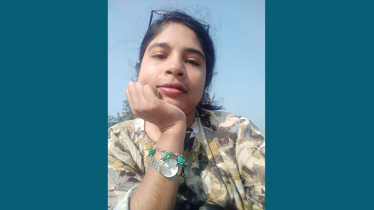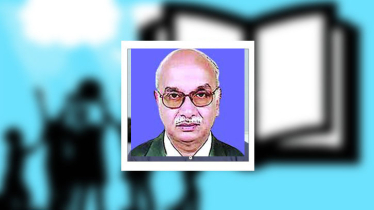মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ভাষা। অর্থপূর্ণ ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’য়ালা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন- 'আল্লাহ মানুষকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' (৫৫ : ২)। ভাষার বিচারে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এর উৎপত্তি ও বিবর্তনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। যার পেছনে রয়েছে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার।
এই যে আমরা প্রতিদিন যে ভাষায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে চলেছি, কখনো ভেবেছেন আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে কেমন ছিল এই বাংলা ভাষা? কীভাবে জন্ম হল এই ভাষার? কীভাবেই বা হাজার বছর ধরে বেড়ে উঠেছে আমাদের প্রাণের ভাষা? অথবা ভেবে দেখুন তো, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ফেসবুক আবিষ্কার হলে কেমন হত সেকেলে মানুষের স্ট্যাটাস! এ সকল প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজতেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।
পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে আমাদের বাংলা ভাষার অবস্থান মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্বে চতুর্থ এবং ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ভাষা। বাংলা সার্বভৌম ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তথা সরকারি ভাষা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আমাদের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কথ্যভাষা বাংলা।
এছাড়া ভারতের ঝাড়খন্ড, বিহার, মেঘালয়, মিজোরাম, উড়িষ্যা রাজ্যগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। ভারতে হিন্দির পরেই সর্বাধিক প্রচলিত বাংলা ভাষা। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে, আমেরিকা ও ইউরোপে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী অধিবাসী রয়েছে। সম্প্রতি লন্ডনে বাংলাকে সরকারিভাবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সিয়েরালিয়নও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই দেশের সরকার। সারা বিশ্বে সব মিলিয়ে ২৬ কোটির অধিক লোক দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ব্যবহার করে।
বাংলা ভাষার ইতিহাস অনেক পুরোনো। যতদূর জানতে পারি, বাংলা ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা বংশের সদস্য। যার উৎপত্তি আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে! খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে এই ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা বংশ থেকে জন্ম নেয় ‘শতম’। এর প্রায় ১০০০ হাজার বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে ‘শতম’ ভাষাটি রূপান্তরিত হয় আর্য ভাষায়। তবে তখনও উপমহাদেশে আর্য ভাষার চল হয়ে উঠেনি। ভারত উপমহাদেশে আর্য ভাষার চল শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে আর্য জাতি আগমনের পর।
উপমহাদেশে আর্য ভাষা চালু হওয়ার পরবর্তী তিনশত বছরে পরিবর্তনের উপমহাদেশীয় হাওয়া লাগে আর্য ভাষায়। প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার শব্দ যোগ হয়ে আর্য ভাষা রূপ নেয় প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ)। আর্য জাতির পাশাপাশি সাধারণ মানুষও আপন করে নেয় এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা। তখন আরো কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে এ ভাষা হয়ে উঠে প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষায় (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ) যা আদিম প্রাকৃত নামেও পরিচিত। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে ৪৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আদিম প্রকৃতের রূপান্তর ঘটে। প্রথমে ‘প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত’ এবং পরবর্তীতে ‘গৌড়ি প্রাকৃত’ ভাষা দু’টির উৎপত্তি হয়। আর এই গৌড়ি প্রাকৃত থেকে ৪৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্ম হয় ‘গৌড়ি অপভ্রংশ’ ভাষার। এই গৌড়ি অপভ্রংশ থেকেই ৯০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে উৎপত্তি হয় বাংলা ভাষার।
শুরুর দিকে অবশ্য বাংলা ভাষা ঠিক শতভাগ এমন ছিল না। ভাষাবিদগণের ভাষায় সে সময়ের বাংলাকে বলা হয় ‘প্রাচীন বাংলা’। এরপর ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আসে ‘মধ্য বাংলা’ এবং ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সেটা রূপ নেয় ‘আধুনিক বাংলা’ ভাষায়। অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা এখন কথা বলি।
এ তো গেল বাংলা ভাষার জন্ম কথা। কিন্তু পরিবর্তনের ধারায় হাজার বছর ধরে কেমন ছিল ভাষাটি? নিচের একটা উদাহরণে তার উত্তর মিলবে।
ইন্দো ইউরোপিয়ান -য়ূস এক্ব্যোম্ স্পেক্যিত্রথে।
শতম -য়ূম এশ্বোম্ স্পেশিএথে।
আর্য- য়ূম অশ্বম্ স্পশ্যাথ্।
প্রাচীন ভারতীয় আর্য- য়ূয়ম অশ্বম্ স্পশ্যাথ্।
আদিম প্রকৃত- তুষ্মে ঘোটকং দৃক্ষথ্।
প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত- তুমহে ঘোটকং দেকখথ।
গৌড়ি প্রাকৃত- তুমহে ঘোড়াঅং দেকখই।
গৌড়ি অপভ্রংশ- তুমহে ঘোড়অ দেকখহ।
প্রাচীন বাংলা- তুমহে ঘোড়া দেখহ।
মধ্য বাংলা- তুমি ঘোড়া দেখ।
এই আধুনিক বাংলা ভাষার সংগ্রহের ইতিহাসও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সাড়া ফেলেছিল। যার সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্বব্যাপী অবগত। এই ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে প্রাণ দিয়েছিলেন বাংলার সূর্য সন্তান শফিউর, রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকেই। যা আমাদের সবারই জানা। তবে অনেকেই যেটা জানে না তা হলো, বাংলা ভাষার জন্য শুধু বাংলাদেশিরা নয়, আন্দোলন করেছেন দেশের বাইরের অনেক মানুষই। পঞ্চাশ এর দশকে ভারতের বিহার রাজ্যের মানভূমি জেলায়ও হয় বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন। ১৯৬১ সালে আমাদের দেশে হয়ে যাওয়া ভাষা আন্দোলনের জোড় ধরে ভারতের শিলচরে বাংলা ভাষার আন্দোলনে ১১ জন শহিদ হন। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো আমাদের ভাষা এবং শহিদদের সম্মানে ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দেয়। শুধু তাই নয় আফ্রিকা মহাদেশের সিয়েরালিওন নামের দেশটিও সম্প্রতি বাংলাকে তাদের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে। পুরো পৃথিবীজুড়ে প্রায় ২৬ কোটির বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। ভাষাভাষীর দিক থেকে প্রথিবীর সপ্তম এবং একই সাথে তিনটি দেশের রাষ্ট্রভাষা “আমার প্রাণের বাংলা”!
অনেকেরই ধারণা বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে। তবে এ বিষয়ে ভাষা বিজ্ঞানীগণ মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন নি। তারা অনেকেই বাংলা র জননী সংস্কৃত বা সংস্কৃতের দোহিতা বাংলা এ কথা মানতে নারাজ। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বেশি এবং ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনের মিল থাকায় একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে সংস্কৃত বাংলার জননী। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে জন্মগ্রহণ করেনি বলে আমাদের সেরা গবেষক ও ভাষা বিজ্ঞানীগণ তা প্রমাণ করেছেন। এদের দলে রয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহসহ আরো অনেকে। তবে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার দূর-আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন মনে করেন বাংলা ভাষার জন্ম দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। এ মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক কথ্য ভাষা থেকে প্রকৃত ভাষার জন্ম। এ প্রাকৃতকে বলা হত প্রাচ্য অঞ্চলের কথ্য ভাষা। পরবর্তী সময়ে এ প্রকৃত থেকে জন্ম হয় মাগধি-প্রাকৃত এবং মাগধী প্রকৃত থেকে জন্ম হয় মাগধী অপভ্রংশের। আর মাগধী অপভ্রংশ থেকেই সৃষ্টি হয় বাংলা ভাষা।
ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষার উদ্ভব বলে মনে করেন। তাঁর মতে, গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষা এসেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যের উত্তরণ ঘটে। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাকে তিনি বলেছেন আদিম প্রকৃত যেখান থেকে আসে প্রাচ্য প্রকৃত। প্রাচ্য প্রাকৃতের পরবর্তীরূপে হলো গৌড়ি প্রাকৃত। আর গৌড়ি-প্রাকৃত থেকে গৌড়ি-অপভ্রংশের জন্ম। ভাষাবিজ্ঞানী এস বি কিথসহ আরো অনেকেই এ মতকে সমর্থন করেছেন।
বাংলা ভাষার উদ্ভব নিয়ে আমরা আরো বিশদভাবে জানতে পারব/যুগের বিবর্তনে আমাদের কাছে যে সব সাহিত্যিক নিদর্শন বিদ্যমান আছে সেগুলো যাচাইয়ের মাধ্যমে। যুগের বিভিন্ন পরিক্রমায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তন লক্ষণীয়। তবে এই পর্বে বাংলা ভাষার উদ্ভব বা জন্ম নিয়ে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীগণের মতামতের ভিত্তিতে একটি ধারাবাহিক বর্ণনার প্রয়াস চালাব।
- ইন্দো- ইউরোপিয় ➤ কেস্তম ও শতম (৩৫০০ খ্রি.পূ.)।
- শতম ➤ আলবানীয়, আরমানীয়, বাল্টো স্লাভানীয় ও আর্য (২৫০০ খ্রি.পৃ)
- আর্য ➤ দারদিক, ইরানীয় ও ভারতীয় (১৫০০-১২০০ খ্রি.পূ.)।
- ভারতীয় ➤ বৈদিক (ঋগ্বেদ) ও প্রাচীন ভারতীয় আর্য (আনুমানিক ১০০০ খ্রি.পৃ)।
- প্রাচীন ভারতীয় আর্য ➤ প্রাচীন ভারতীয় কথ্য আর্য (আদিম প্রাকৃত: ৮০০ খ্রী. পূ.)।
- প্রাচীন ভারতীয় কথ্য আর্য ➤ প্রাচীন শৌরসেনী, আশোক লিপীর ভাষা, প্রাচীন উদীচ্য, পালি ও প্রাচীন প্রাচ্য (খ্রি.পৃ. ৪০০)।
- প্রাচীন প্রাচ্য ➤ প্রাকৃত, প্রাচীন সিংহলি, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, অর্ধ মাগধি প্রাকৃত, মাগধি প্রাকৃত, গৌড়ি প্রাকৃত (আনু: ২০০ খ্রি.পূ.)।
- গৌড়ি প্রাকৃত ➤ মাগধি অপভ্রংশ ও গৌড়ি অপভ্রংশ (আনু: ৪০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দ)।
- গৌড়ি অপভ্রংশ ➤ বিহারি, প্রাচীন উড়িয়া ও বঙ্গ কামরূপী (আনু: ৫০০ খ্রিস্টাব্দ)।
- বঙ্গ কামরূপী ➤ অসমিয়া ও বাংলা (৬০০ খ্রিস্টাব্দ)।
আমরা এখন বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাস নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব। বাংলা ভাষার ইতিহাসকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:
১। প্রাচীন বাংলা (৯০০/১০০০-১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ)- ‘চর্যাপদ’ ভক্তিমূলক গান এই সময়কার লিখিত নিদর্শন। এই সময় আমি, তুমি ইত্যাদি সর্বনাম এবং ইলা, ইরা ইত্যাদি ক্রিয়া বিভক্তির আবির্ভাব ঘটে।
২। মধ্য বাংলা (১৪০০-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)- সময়ে গুরুত্বপূর্ণ লিখিত নিদর্শন চন্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। শব্দের শেষে ‘অ’ ধ্বনির বিলোপ, যৌক্তিক ক্রিয়ার প্রচলন, ফারসি ভাষার প্রভাব এই সময়ের সাহিত্যিক লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ভাষাবিদ এই যুগকে আদি ও অন্ত্য এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।
৩। আধুনিক বাংলা (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান)- এই সময়ে ক্রিয়া ও সর্বনামের সংক্ষেপন ঘটে। যেমন: তাহার→ তার, করিয়াছিল→ করেছিল ইত্যাদি।
যুগের পরিক্রমায় প্রাচীন যুগে বাংলার নবজাগরণের সময় বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত ভাষা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিল। সংস্কৃত থেকে যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় যোগ করা হয়, তাদের উচ্চারণ অন্যান্য বাংলা রীতি মেনে পরিবর্তিত হলেও সংস্কৃত বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়।
মধ্যযুগে বাংলা ভাষার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন বাংলার মুসলিম শাসকগোষ্ঠী। ফারসির পাশাপাশি বাংলাও বাংলার সালতানাতের দাফতরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল এবং ব্যাপকহারে ব্যবহার হতো। এছাড়াও প্রত্ন বাংলা ছিল পাল ও সেন সম্রাজ্যের প্রধান ভাষা।
আধুনিক যুগ অর্থাৎ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নদিয়া অঞ্চলে প্রচলিত পশ্চিম- মধ্য বাংলা কথ্য ভাষার উপর ভিত্তি করে আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক বাংলা শব্দ ভান্ডারে মাগধী প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত, ফারসি, আরবি ভাষা এবং অস্ট্রো এশীয় ভাষাসমূহ সহ অন্যান্য ভাষা পরিবারের শব্দ স্থান পেয়েছে।
অষ্টাব্দ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ব্যাকরণ রচনার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ১৭৩৪ থেকে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভাওয়াল জমিদারিতে কর্মরত অবস্থায় পর্তুগিজ খ্রিষ্টান পুরোহিত ও ধর্মপ্রচারক ম্যানুয়েল দ্য আসুম্পসাও সর্বপ্রথম ভোকাবোলারিও এম ইডিওমা বেঙ্গলা নামক বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন। ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড নামক এক ইংরেজ ব্যাকরণবিদ ‘অ্যা গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’ নামক গ্রন্থে আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। যেখানে ছাপাখানার বাংলা হরফ প্রথম ব্যবহৃত হয়।
বাংলা সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ‘গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ’ নামক একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ভাষাকে বিশ্ববাজারে সমাসীন করতে আরও যাদের অবদান অপরিসীম তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম। বাংলা ভাষাকে বোধগম্য করে তোলার জন্য তিনি বিরাম চিহ্নের উদ্ভব ঘটান। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, প্যারাচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ অনেকের অবদান অনস্বীকার্য।
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পাওয়া আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন বাংলা ভাষাকে যুগ উপযোগী করে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করতে আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। জাতিসংঘ যেহেতু বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এবং বেশ কয়েকটা দেশ বাংলাকে তাদের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং আমাদেরও বিশেষ কিছু করণীয় থাকা জরুরি। নিম্নে বাংলা ভাষার তাৎপর্য বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরছি-
∎ নির্দিষ্ট দিবসের (২১ ফেব্রুয়ারি) মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অফিস আদালতে ব্যবহৃত ভাষা বাংলা হওয়া জরুরি।
∎ শুদ্ধ প্রমিত মান ভাষা ব্যবহারে আমাদের যত্নবান হওয়া।
∎ আঞ্চলিক বা উপভাষা সংরক্ষণের জন্য আলাদা অভিধান গ্রন্থ রচনা করা।
∎ বাংলা-ইংরেজি সংমিশ্রণ (বাংলিশ) না করে শুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রতি সতর্ক হওয়া।
∎ পরিবেশের সাথে উপযোগী ভাষা ব্যবহার করা।
∎ বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যকে আমাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করা।
∎ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষ করে সাপ্তাহিক পবিত্র জুম্মার দিনে বাংলা খুৎবার প্রচলন করা।
∎ বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বিদেশি ভাষায় প্রদান করা বক্তব্য বাংলা অনুবাদ করা।
∎ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে জাতিসংঘের মত জায়গায় বাংলা ভাষণ দান করা।
∎ যে সকল প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষাকে বিকৃত করে প্রচার করে তাদেরকে সরকারের তরফ থেকে শুদ্ধ বাংলা প্রচারের জন্য অনুপ্রাণিত করা।
∎ বাংলা একাডেমিসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করে সে সকল জায়গায় লোকবল বৃদ্ধিসহ আর্থিক বরাদ্দ করানো।
ক্ষুদ্র পরিসরে উপরিউক্ত শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করা হলে তার যথার্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হলে আমাদের প্রাণের ভাষা মায়ের ভাষা বিশ্ব দরবারে আপন মহিমায় আসন করে নেবে। মা জননী বাংলা দীর্ঘজীবী হোক এই প্রত্যাশায় ইতি টানলাম।
লেখক:
আলিমুল হক
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
কেবিএস দাখিল মাদ্রাসা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
E-mail: [email protected]
"এই বিভাগে প্রকাশিত মুক্তমতের সকল দায়ভার লেখকের নিজের। ক্যাম্পাস বাংলা কোনভাবেই এই বিভাগের লেখক কিংবা লেখার বিষয়বস্তুর দায়ভার নিচ্ছে না।"